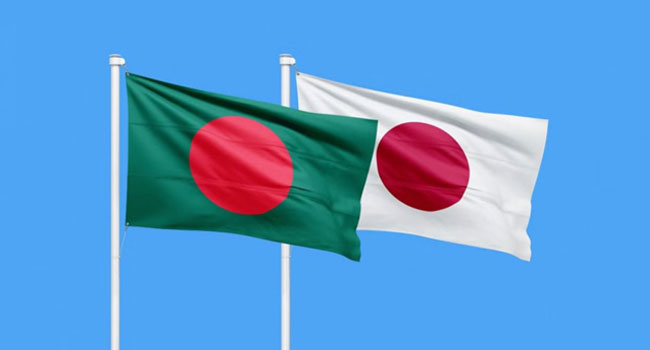
জাপান আগের শতাব্দী থেকে সংস্কার শুরু করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ১৮৬৮ সালে জাপানে মেইজি সম্রাটের আমলে ব্যাপক সংস্কার শুরু হয়। ১৮৬৮ সালে মেইজি যুগ। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাপান সরকার চিন্তা করে বাইরেও দুনিয়া আছে। এর আগে জাপান মনে করত তারাই সব। বাইরের দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিজেদের চিন্তার জগতে এক ধরনের পরিবর্তন হয়। তারা ভাবতে থাকে, টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে হলে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। তারা ভাবতে থাকল- বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ এবং তাদের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা জানতে না পারলে টেকসই উন্নয়ন ও স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা সত্যিই কঠিন। দেশের বিশ^বিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি দিয়ে জাপান বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সফরে পাঠায়। তাদের নির্দেশনা দেয়া হলো- তোমাদের যাবতীয় ব্যয় রাষ্ট্র নির্বাহ করবে। তোমরা শুধু সংশ্লিষ্ট দেশের যত ভালো গুণ এবং মন্দ গুণ আছে তা লিস্ট করে আনবে, জেনে আসবে তাদের সাফল্যের কাহিনী আর বিফল হওয়ার কারণগুলো।
নির্দেশ মোতাবেক ছাত্ররা পাঁচ বছর সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থান করে সে দেশের ইতিহাস, মানব চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং তাদের ভালো-মন্দ গুণগুলো তালিকা করে নিয়ে আসে। পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে এসব তথ্য তারা পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করে। এরপর দুই বছরের জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিশন গঠন করে কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হলো জাপানের শিল্পায়ন তথা বিষয়-ভিত্তিক উন্নয়নে প্রযোজ্য নীতিমালার, গাইড লাইন ইত্যাদি প্রস্তুত করার। এ ছাড়াও ধর্মনীতি, আইননীতি এবং অন্যান্য খাতের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ভালো হবে তার আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপত্র বা সুপারিশমালা তৈরি করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। অর্থাৎ বাইরের দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা তাদের দেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। কি করা যাবে, কি করা যাবে না- এসব বিষয় নিয়ে পৃথক গাইডবই প্রস্তুত করা হয়।
১৮৯০ সালের মধ্যে জাপান সরকার নিজেদের জন্য প্রযোজ্য ও অনুসরণীয় একটি সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে সক্ষম হয়। এ দীক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তারা নতুন পথচলা শুরু করে। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাদের শিল্পায়ন, কৃষি, বাণিজ্য তথা অর্থনীতির দিকগুলো পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে তোলে। জাপান নতুন এক উদ্দীপনা নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ঢেলে সাজায়। এরপর শুরু হয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ। তারা খুব অল্প দিনের মধ্যে চমৎকার অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ওই সময় জাপানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি উচ্চ মাত্রায় চলে যায়। শিক্ষার হার এবং মান বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্যবিমোচনে অগ্রগতি হয়। জাপানের পণ্য ও সেবা রফতানি বেড়ে যায়। বাইরের দেশগুলোর সাথে জাপানের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিস্ময়কর উন্নতি হয়। অর্থাৎ এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেখানে জাপান পিছিয়ে থাকল। বাইরের দেশগুলোও জাপানের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। বিদেশ থেকে প্রচুর বিনিয়োগ জাপানে আসতে শুরু করে।
সব কিছু ভালোভাবে চলছিল। কিন্তু একসময় জাপানে সামরিকীকরণ হতে শুরু করে। সেনাবাহিনী প্রশাসনে কিংবা ক্ষমতার সম্মুুখ সারিতে চলে আসে। জাপানিরা মূলত সামুরাই জাতি বিধায় সবসময় এক ধরনের যুদ্ধংদেহি মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে। এক সময় দেখা গেল, রাজা নিরীহ রাজার মতো আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে চলে গেছে। একপর্যায়ে সেনাবাহিনীর মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হতে থাকে। দুই-তিন বছর পরপর জাপানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে থাকল। ফলে জাপানের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। বেসামরিক মন্ত্রীদের সামরিক বাহিনী নানাভাবে পর্যুদস্ত করতে থাকে। সেনাবাহিনী ঘিরে গড়ে ওঠা উগ্র জাতীয়তাবাদ জাপানের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা ব্যাহত করে।
১৯১৩ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত যে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে জাপানি সেনাকর্মকর্তারা ততটা সামনে না এলেও ১৯৩১ সাল পর্যন্ত জাপানে অন্তত ১৩-১৪টি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জাপানের একজন প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেয়ার সময় তাকে ছুরিকাঘাত করে মেরে ফেলা হয়। জাপানের অর্থনীতি এ সময় অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। কারণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উগ্র সামরিক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩৯ সালে শুরু হওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সেনাবাহিনী সম্মুখ সারিতে চলে আসে। সেই সময় জাপানের সেনাবাহিনী নিজেদের মনে করতে লাগল, তারা বিশে^র অন্যতম শক্তিশালী সেনাবাহিনী। জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদী হিটলারের সাথে জাপানি সেনাবাহিনীর যোগসূত্র তৈরি হয়। ১৯৪২ সালে জাপানি সেনাবাহিনীর একটি দল পার্ল হারবারে মার্কিন জাহাজের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে। ওই আক্রমণ করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে। এ আক্রমণ ছিল অতর্কিত আক্রমণ। যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর ভীষণ ক্ষেপে যায়। জাপানের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ যুদ্ধনীতি ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপন করে। ওই আক্রমণের ফলে মিত্রবাহিনী আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হচ্ছে জাপান। জার্মানিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সেই ক্ষতির পরিমাণ জাপানের মতো এত বেশি ছিল না। পার্ল হারবারে মার্কিন জাহাজের ওপর জাপানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে সেই বছর বিশেষ মারণাস্ত্র তৈরির প্রকল্প নেয়। তারা দৃঢ় সঙ্কল্প হয় যে, এমন একটি মারণাস্ত্র তৈরি করবে যাতে জাপানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া যায়। ওই উদ্যোগের ফল হচ্ছে অ্যাটম বোমা। ১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র অ্যাটম বোমা তৈরি করে, ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হিরোশিমা ও ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে হাজার হাজার মানুষ চোখের পলকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং এর তেজষ্ক্রিয়ায় কয়েক প্রজন্ম পঙ্গুত্ব বরণ করে। টোকিও পারমাণবিক বোমার বিষয়টি জানতে পারে কয়েকদিন পর। তারা মনে করেছিল, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল সেটি সাধারণ কোনো বোমা ছিল। পারমাণবিক বোমার ভয়াবহতা জাপানিদের যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে। তারা চাইছিল না আর কোনো পারমাণবিক বোমা তাদের জনগণের ওপর ফেলা হোক। জাপান যুদ্ধবিরতি করতে সম্মত হয়। মূলত এ দু’টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। কারণ জাপান কার্যত আত্মসমর্পণ করে। প্রতিপক্ষ তখন বিজয়ী হয়ে গেল। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে।
দ্বিতীয় বিশ^যুদ্ধে জাপানের এই যে করুণ পরিণতি তা জাপানের জন্য ‘শাপে বর’ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সামরিক শক্তিবলে বিশ্ব জয় করার চ্যালেঞ্জ না নিয়ে অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নিলো। ১৯৩০ সাল থেকে জাপানিরা শিল্পের ওপর জোর দিলেও তারা সামরিক শক্তিবলে বিশ্বজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিল। তাদের সেই কৌশল যে সঠিক ছিল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করুণ পরিণতি সেটি বুঝিয়ে দেয়। ১৯৪৫ সালে জাপান সারেন্ডারের পর জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থারকে প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হলে তিনি টোকিও ট্রায়ালের উদ্যোগ নিলেন। তিনি এ ট্রায়ালের মাধ্যমে জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীসহ যারা যুদ্ধের জন্য দায়ী ছিলেন তাদের ফাঁসি হয়। ওই বিচারের মাধ্যমে জনগণের কাছে এমন একটি বার্তা দেয়া হলো যে, জাপান আর কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখবে না। ভবিষ্যতে আর কোনো যুদ্ধে জড়ানো হবে না- এমন একটি ধারা জাপানি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এটিকে ৯ নম্বর ধারা বলা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, জাপান নিজস্ব সেনাবাহিনী লালন করবে না। তারা যুদ্ধ উপলক্ষে বিদেশে কোনো সৈন্য পাঠাবে না। এরপর জাপানিদের শিল্পে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেয়া হয়। একটি যুদ্ধংদেহি জাতিকে রাতারাতি শিল্পায়নের দিকে নিয়ে আসা হলো। দেশের বাইরে জাপানের যেসব উপনিবেশ ছিল সেখান থেকে জাপানি সৈন্যরা সব দেশে ফিরে আসে। এদের বিভিন্ন কলকারখানায় কাজের ব্যবস্থা করা হলো। একটি যুদ্ধবাজ জাতি রাতারাতি শিল্প উন্নয়নে শান্তিপ্রিয় জাতিতে পরিণত হলো।
১৯৫১ সালে কোরিয়ায় একটি যুদ্ধ হয়। কোরিয়ার সাথে জাপানের সম্পর্ক হচ্ছে ‘সাপে নেউলে’। এক সময় জাপানিরা কোরীয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ান যুদ্ধের যত ব্যবসায় এবং অস্ত্রপাতি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় সব জাপানকে পাইয়ে দেয়া হলো। সেই সময় জাপান ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং দরিদ্র একটি জাতি। পুরুষরা কাজ পাচ্ছিল না। তারা ঘরে বসে থাকত। মেয়েরা গিয়ে শাপলা শালুক খুঁজত। এভাবে অত্যন্ত দীনহীনভাবে জীবনযাপন করছিল। চুরি ও অসামাজিক কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যেত, বারান্দায় কাপড় শুকাতে দিয়ে ঘরে আসার আগেই সেই কাপড় চুরি হয়ে গেছে। জাপানিদের নৈতিকতা সাঙ্ঘাতিকভাবে বিপর্যয় ঘটে। জাপানি জনগণকে বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ দেয়া হলো। তারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাদের আর্থিক অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হলো। ১৯৫৫ সালে জাপানি কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল, আমরা যুদ্ধের পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছি। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে ঠিক একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করি। দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে ঋণখেলাপি দেশে পরিণত হয়েছিল। উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেশটির সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সেই অবস্থা থেকে তারা আবারো ঘুরে দাঁড়ানোর পর্যায়ে চলে এসেছে।
এখন প্রশ্ন হলো, আমরা বাংলাদেশীরা জাপানের এ বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্য থেকে কী শিক্ষা নিতে পারি? জাপানের এই অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে দেশটির নেতৃত্বের সততা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, জাতির প্রতি নেতাদের কমিটমেন্ট। এ ছাড়া জাপানের বিচারব্যবস্থাও অত্যন্ত শক্তিশালী। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের জীবন-জীবিকার অর্থনীতি তথা দক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলার প্রতি কমিটমেন্ট ছিল লক্ষ করার মতো। আমেরিকার পলিসি জাপানের উন্নয়নে বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে। জাপান একটি ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ। তাই তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদেশেও প্রচুর সংখ্যক শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছে, রিলোকেট করেছে।
জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এটিই শিক্ষা নিতে পারি, নেতৃত্বের সর্বোচ্চ সতর্কতা, আন্তরিকতা, দেশের প্রতি কমিটমেন্ট এবং জনগণের প্রতি ভালোবাসা থাকলে একটি দেশ উন্নতি অর্জন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোয় সরকার অনুগমনের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ সুশাসন নিশ্চিত হলে, ঘুষ-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠে দায়িত্ব পালনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশও জাপানের মতো অর্থনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় সফল হবে এবং অর্থবহ উন্নয়ন সাধন করতে পারবে।